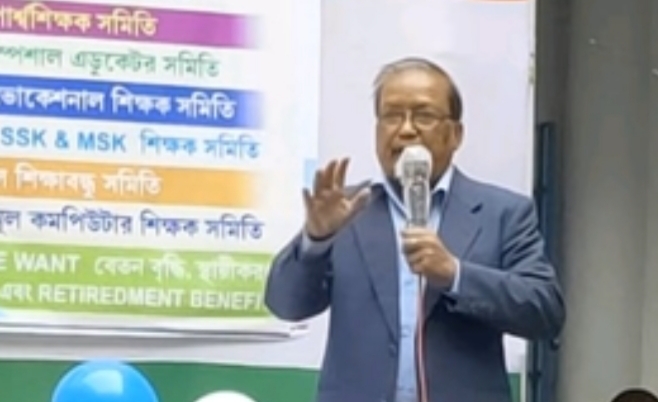Confidence to Police পুলিশে আস্থা
🟣 দিলীপ রঞ্জন ভাদুড়ী
➡️ বগটুই কাণ্ডে মহামান্য কলকাতা হাই কোর্ট প্রথমে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের গঠিত সিটকে তদন্ত করার সুযোগ দিয়েছিলেন।মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বহু আশা করে এই তদন্তদল গঠন করেছিলেন। যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও শক্তিশালী ছিল এই দল। কিন্তু, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মান রক্ষা করতে পারলেন না। মহামান্য প্রধান বিচারপতি কেস ডায়েরী ও পুলিশের রিপোর্ট দেখে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। জনমানসে সিটের তদন্ত কোন মতেই আস্থা ফেরাতে পারবে না নিশ্চিত হয়ে সিবিআই কে তদন্তের নির্দেশ দিলেন। বললেন, রাজ্য পুলিশকে সহযোগিতা করতে হবে।
পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকারের হার বেশি। দলাদলি ঝগড়াঝাটি, কথা কাটা কাটি, মিছিল, মিটিং, অনশন, কথায় কথায় পথ অবরোধ, রেল অবরোধ, নানা হুজ্জুতির শেষ নেই। কে কত জনপ্রেমী দেখাবার নাটক, দেখতে দেখতে মানুষ হয়রান। মহামান্য হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই মামলা রুজু করেছিলেন ও রায় দান করেছেন। রাজনৈতিক দলের কোন কোন নেতা এমন ভাব দেখাচ্ছেন যে তাঁরা যেন যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন! পশ্চিম বঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এক পক্ষ রুদালি, রুদালি বলে গলাবাজি করছেন। এ সব বাক যুদ্ধের সময় এটা নয়। বহু বড় বড় নেতা সিবিআই ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তদন্তের মানের তুলনা করেছেন। কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল চুরি, নারদা কাণ্ডে বিরোধী দল নেতাকে গ্রেপ্তার না করা এসব নিয়ে কথা বলছেন। সাংসদ ও বিধায়করা সবাই জানে কোথায় গিয়ে কি আটকে আছে। তারমধ্যে শাসক দলের কয়েকজন আছেন। আসলে খালি চোখে আমরা যা দেখি তা একদম ঠিক নয়। কেন্দ্রে ও রাজ্যে তালমিলের কোন অভাব নেই। সব চাইতে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে পশ্চিম বঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সমতুল্য বর্তমান ভারতে কজন আছেন। বহু প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রের কাছে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। ঝগড়াঝাঁটি যা দেখি, এগুলো রাজনীতির অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল ও রেপ্লিকা চোরেরা কি ভাবে চুরি করেছিল সেটা নিয়ে জেলা পুলিশ ও সিবিআই একমত নয় বলেই শুনেছি। রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগ ও জেলা পুলিশ প্রথম দিকে তদন্ত করে কোন সূত্র বের করতে পারেনি বলেই শুনেছি। তাহলে, সিবিআই নোবেল উদ্ধার করতে পারেনি বলে দোষী নয়। এই ধরনের দুষ্প্রাপ্য সম্পদ চোরা কারবারীরাই করে থাকে। ভিতরের লোক জড়িত না থাকলে এ চুরি সম্ভব ছিলনা। এসব আলোচনা মানুষের মনে অনাস্থা আনবার জন্য বলে। সিবিআই নেটওয়ার্ক যতটা বিস্তৃত, কোন রাজ্য পুলিশের ততটা নয়। বারাণসী কাশী বিশ্বনাথ মন্দির থেকে অন্নপূর্ণা মূর্তি চুরি হয়েছিল ১০০ বছরের আগে। বিদেশে পাচার হয়ে গিয়েছিল। বিদেশের সংগ্রহশালায় ওটা পেয়ে ভারত সরকার ফিরিয়ে এনেছেন। এ রকম বহু চুরি যাওয়া সম্পদ ফেরত এনেছেন। কিন্তু, প্রচার সে ভাবে হয়নি। আমাদের আশা জাগিয়ে রাখতে হবে। যাঁরা এসব বলেন যথেষ্ট শিক্ষিত এবং রাজনৈতিক দক্ষ ব্যক্তিত্ব। তাঁরা সব জানেন রাজনৈতিক ভাবে বলতে হয় বলেন। সিবিআই, ইডি এসব কেন্দ্রীয় পুলিশ আর সিআইডি, ই বি, জেলা পুলিশ হল রাজ্য পুলিশ। উভয়েই পুলিশ। কাজ কর্ম, তদন্ত পদ্ধতিতে ফারাক আছে। কারও অবাধ স্বাধীনতা নেই। একটা জায়গায় সবাইকে থামতেই হয়। ফলে থমকে থাকে অনেক সত্য উদঘাটন। কেন সবাই জানেন, খুলে বলার প্রয়োজন নেই। তাই এসব বিতর্ক কোন কিছু ভাল ফল দায়ক নয়। ব্রিটিশ আমলের আইন ও আয়ারল্যান্ড ধাঁচের পুলিশি ব্যবস্থায় আমরা কাজ করি। জনগণের মন এই পদ্ধতিতে কোনদিন জয় করা সম্ভব নয়। বিচার পদ্ধতির দীর্ঘ সূত্রিতার কোন আশু সমাধান নেই। বর্তমান সময়ে মূল সাক্ষী বিগড়ে যাওয়া খুব সহজ ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। ফলে শুধু পুলিশ নয় সামগ্রিক চিত্রটাই বেশ হতাশা ব্যঞ্জক।
সিবিআই কে তদন্ত ভার দেওয়ার উদ্দেশ্য জনমানসে পুলিশের ভাব মূর্তি উজ্জ্বল করা ও পুলিশ সম্বন্ধে মানুষের আস্থা ফেরানো। পুলিশ বলতে আমরা যা বুঝি, তাঁর প্রসব হয়েছিল ব্রিটিশ রাজের হাতে। তখন থেকেই ধারাবাহিক ভাবে পুলিশ যে ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তার কলঙ্কিত ইতিহাসের রেশ থেকে পুলিশ মুক্তি পায়নি। ইতিহাস তুলে ধরার আগে জানতে হবে পুলিশ কমিশন ও পুলিশ আইনের কথা। আমরা পুলিশের পাঁচ আইনের কথা বলি। ১৮৬১ সালে পাঁচ নম্বর আইন বলে পুলিশ কে সংগঠিত ও আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। প্রতিটি প্রদেশের পুলিশ বাহিনীর প্রধান হল একজন করে ইন্সপেক্টর জেনারেল। জেলার ভার দেওয়া হয় পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের উপর। নিম্ন পুলিশ বলতে ইন্সপেক্টর ও তাঁর নিম্নস্তরের পুলিশের বাহিনী কে বলা হয়েছে। বেঙ্গল পুলিশ রেগুলেশন এই আইন মোতাবেক রচিত হয়েছিল। নিম্নস্তরের জন্য খুব কঠোর এই বিধি। বেঁধে ফেলা হল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার আইন ও রেগুলেশন জালে। উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত করা, বিদ্রোহীদের দমন পীড়ন করা, ব্রিটিশদের সুরক্ষা দেওয়া। নিম্নস্তরে ভারতীয়দের আস্তে আস্তে নেওয়া শুরু হয়েছিল। ১৮৬৫ সালে প্রথম পুলিশ কমিশন গঠন হয়। উদ্দেশ্য ছিল পুলিশ বাহিনীকে সরকারের কর্মচারী হিসেবে আইন প্রয়োগ করতে হবে, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করতে তদন্ত করতে হবে। এই শুরু। স্বাধীনতা কামী ভারতীয়দের দুটিস্তর ছিল। একদল বাপুজির অহিংসা ধর্মী ও অন্যান্যরা ছিলেন চিরবিদ্রোহী ও সংগ্রামে বিশ্বাসী। মধ্যপন্থীরাও ছিলেন। বিচার ব্যবস্থায় জুড়ি বিধি ছিল। রীতিমতো বিচারব্যবস্থা শাসকের পক্ষে ছিল। ১৮৬৪ সালে চালু হয় হুইপিং এ্যাক্ট। পুলিশ পেয়ে যায় লাঠির অধিকার। কারন, ভারত ছিল ইংরেজদের উপনিবেশ। তাই ভারতের জন্য আর এক উপনিবেশ আয়ারল্যান্ডে চালু পুলিশ বিধি ব্যবস্থা বেছে নেওয়া হয়েছিল। পুলিশ হয়ে উঠে উৎপীড়ক। তখন থেকেই ভারতীয় বিশেষ করে বাঙ্গালীদের কাছে জন্মলগ্ন থেকেই কালিমালিপ্ত হয়ে যায়। আমি পরাধীন ভারতের পুলিশ নিয়ে কিছু খুলে বলতে চাইছি না। আমরা ইতিহাসে পড়েছি যে আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমন করেন তখন ভারতীয় রাজন্যবর্গ এক হয়ে বিদেশী আক্রমন রুখে দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নি। ঠিক একই ভাবে ভারতীয়রা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লড়তে পারেননি। সবাই বিচ্ছিন্ন ভাবে সংগ্রাম করেছে। কেউ অহিংস আন্দোলন, কেউ হিংসা আন্দোলন নানা ভাবে বিচ্ছিন্ন ভাবে লড়াই করেছেন।
বেনেরা ভালোই বুঝে গিয়েছিল যে ভারতে তাঁদের পক্ষে বেশিদিন শান্তিতে বসবাস করা সম্ভব নয়। তাঁরা অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী কংগ্রেসের সাথে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভারতকে দুর্বল করতে ভারতকে ধর্মান্ধতা প্রশ্রয় দিয়ে ভারতকে টুকরো করে দিয়েছিল। ভারত স্বাধীনতা পেয়েছিল যুদ্ধ করে নয় আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে। তাই জাতীয়তাবাদ কাকে বলে, এই নিয়ে এক নয় ভারতবাসী। ভারত স্বাধীন হবার পরেও পুলিশের ব্যবহার শাসকের স্বার্থে চলা শুরু করল। পুলিশকে সমাজের কাছে বিশ্বাস যোগ্যতা দিতে পারল না। পুলিশের দানবীয় ভাবমূর্তিটি সবার মাঝে রয়ে গেল। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৭ সাল কৃষক বিদ্রোহ বা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শুরু হয় তেভাগা আন্দোলন। যদিও এই আন্দোলনের শুরু আগে থেকেই শুরু হয়েছিল কিন্তু বাস্তবতা পায় এই সময়। দুই বাংলায় আন্দোলন শুরু হয় প্রবল ভাবে। দাবি অত্যন্ত ন্যায্য। কৃষকরা বীজ ও চাষ করত কিন্তু অর্ধেক ফসল তুলে দিতে হত জোতদারের হাতে। জোতদার কোন ভাগ ছাড় দিতে রাজি হতনা। জোতদার হল প্রকৃত জমির মালিক ও চাষীর মধ্যবর্তী দালাল। মধ্যস্বত্বভোগী। এই সময় কংগ্রেস শাসকরা পুলিশকে এই আন্দোলন দমন করার কাজে ব্যবহার করেছিল। ১৯৪৭ সালে পুলিশ আন্দোলন কারীদের দমাতে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে চাষীদের উপর দু'দফায় গুলি চালনা করে প্রায় ৭০ জন চাষীকে হত্যা করে। তখনও ভারত স্বাধীনতা পায় নি। স্বাধীনতার প্রাক মুহূর্তের প্রতিচ্ছবি। ভারত ও পাকিস্তান বিভাগে এসেছিল জাতি দাঙ্গা। পুলিশের ভূমিকা কি ছিল, ইতিহাস তার সাক্ষী। বঙ্গ বিভাগে শরণার্থীদের দুর্দশার কথা সবাই জানে। মরিচঝাঁপিতে শাসকের পরিচালনায় যে গণহত্যা হয়েছিল তাতে পুলিশ ছিল হত্যাকাণ্ডের মুখ্য ভূমিকায়। শাসক ছিল ব্রিটিশ শাসকের ভূমিকায়। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরী অবস্থা জারি করে পুলিশকে স্বৈরাচারির ভূমিকায় ঠেলে দিয়েছিল। সে সময় রাজনৈতিক দলগুলো চারু মজুমদারের নেতৃত্বে গড়ে উঠা নকশাল আন্দোলনের মুখে রাজনৈতিক মোকাবিলার সাহস দেখায় নি। পুলিশকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই হিংসাশ্রয়ী আন্দোলন দমনের জন্য। পুলিশ ভাবতে শিখেছিল নকশাল মাত্রেই শ্রেণী শত্রু ও নকশাল পুলিশকে মূল শ্রেণী শত্রু বলে ঘোষণা করেছিল। ওরাও বহু পুলিশকে হত্যা করেছিল এবং পুলিশ নকশাল আন্দোলন দমনের নামে বহু নিরপরাধ ব্যক্তিদের রক্ত নদীর বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। বলতে গেলে পুলিশ নকশাল আন্দোলন দমন করে দিয়েছিল। এই পুলিশের ভয়ঙ্কর রূপ কি বৃহৎ সমাজ খুব সহজে ভুলতে পারে। জমির চাষী বাম আমলে তেভাগা আন্দোলনের সফলতা পায়। পুলিশের আগে একটি সংগঠন ছিল। বাম আমলে আর একটি নীচু তলার পুলিশদের সংগঠন স্বীকৃতি পায়। ফলে পুলিশের মধ্যে বাম ও বাম বিরোধী সংগঠনের সৃষ্টি হয়। কিন্তু, এই দুটি সংগঠন কিন্তু কোন শ্রমিক সমিতি বা কর্মীসঙ্ঘ ছিল না। এই দুই সংগঠনের কর্তা ব্যক্তিরা কোন কাজ না করে মুরুব্বিয়ানা করত। এই ভাবেই পুলিশের মধ্যে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে। ৮০-র দশকে এর পরিপূর্ণতা আসে। পুলিশ বুঝে যায় কি করলে সরকারের সহানুভূতি পাওয়া যাবে ও মনমতো পোস্টিং পাওয়া যাবে। উপরমহল ও এর বাইরে ছিলেন না। বহু সিনিয়র কে টপকে জুনিয়ররা উচ্চপদে ঠাঁই পেতে শুরু করে। পুলিশের মনোবল ভেঙে যায়। একটা সময় ছিল জেলার পুলিশ সুপারকে টপকে কোন কাজ করার সাহস ছিলনা অধঃস্তন পুলিশ কর্মচারীদের। তখন নীচু তলার পুলিশের ভাল মন্দ বিচারের মালিক ছিলেন পুলিশ সুপাররা। ক্রাইম কন্ট্রোল করতে না পারাটা ছিল লজ্জার। আস্তে আস্তে এই ব্যবস্থাটায় দৃষ্টি ভঙ্গী পাল্টে গেল। শাসকদের নেক নজরে থাকাটাই পুলিশের মুখ্য কাজ হয়ে গেল। পুলিশের রেগুলেশনে পুলিশের দুটি স্তর। নিম্ন স্তর হল ইন্সপেক্টর ও তার নিম্ন পুলিশ কর্মচারীগন। উচ্চ স্তর হল ডিএসপি ও উর্ধতন পদাধিকারিরা। শান্তি শৃঙ্খলা, অপরাধ রোখা, তদন্ত করা, গ্রেপ্তার করা, টহল দেওয়া, গোপন সংবাদ, আগাম সংবাদ সংগ্রহ করা ইত্যাদি যাবতীয় মূল পুলিশের কাজ গুলো নিচুস্তরের পুলিশের করতে হয়। এঁদের কাজের উপর পুলিশের ভালোমন্দ সামগ্রিক ভাবে বিচার হয়। এঁরা এখন নির্ভয়ে কাজ করতে পারছেন না। সব ব্যাপারে কি করবেন আর কি করতে পারবেন না এটা তাঁদের মধ্যে প্রশ্নের সৃষ্টি করে। নিরপেক্ষতার তো প্রশ্নই নেই, সঠিক কাজ কি সেটাই করার সাহস নেই। আকছার মিথ্যে কেস হয় কিন্তু জেনে বুঝেও ন্যায়ের পক্ষে যেতে পারেন না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী পুলিশের সংগঠন তুলে দিয়েছেন। ভাল কাজ করেছিলেন বলেই মনে করি। তিনিও উপলব্দি করেছেন যে পুলিশের মনোবল বাড়াতে হবে। স্বাধীন ভারতের প্রথম পুলিশ কমিশন ব্রিটিশ রাজের পুলিশী ব্যবস্থার সংস্কার চেয়ে ছিলেন। ওই পর্যন্তই। বিভাগ বেড়েছে, কাজ বেড়েছে, কাজের পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে কিন্তু পুলিশের নিচুস্তরে সুশিক্ষিত পুলিশের সংখ্যা দিন দিন কমছে। তার বদলে সিভিক ভলান্টিয়ার, হোম গার্ড, এন ভি এফ, এসব দিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে। জনসংখ্যা অনুযায়ী পুলিশ কনস্টেবল পোস্টিং দরকার। এখন সুপারভাইজার অফিসারদের সংখ্যা যথেষ্ট। কিন্তু, তাঁরাও ঠিক ভাবে দেখভাল করেন না। এক ঢিলে ঢালা ভাবে কাজ চলছে। চলছে চলুক। তাতে কোন মাথা ব্যথা নেই। হঠাৎ রাজনৈতিক কারণেই হোক বা ব্যক্তিগত কারনেই হোক নীচু তলার পুলিশের প্রতি মানুষের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। অভিযোগ হচ্ছে। এটা সামগ্রিক ভাবে পুলিশের প্রতি মানুষের অনাস্থা ও পুলিশের মনোবল ভাঙার জন্য যথেষ্ট। পুলিশ বিভাগের লজ্জারও।
পুলিশে ব্রিটিশ আমল থেকেই, ট্রিগার হ্যাপি পুলিশ কিছু আছে। তাঁদের এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট বলা হয়। তাঁদের অসীম সাহস ও পুলিশ বিভাগে যথেষ্ট সমাদর আছে। অনেকেই গ্যালান্টারি পদক পেয়েছেন। কিন্তু, মানবাধিকার কমিশন সৃষ্টি হবার পর পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের পরিধি অনেক কমে গেছে। আইন কানুন অনেক বদলে গেলেও পুলিশের মানসিকতা ব্রিটিশ যুগেই আছে। ইতিহাসবিদ সুগত বসু বলেছেন, মানুষের দৈনন্দিন কাজ কর্মে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু, আমরা এটাকে বর্তমান সময়ে এড়িয়ে ক'জন চলতে পারি। সরকার যেই থাকুক, সরকারী কর্মচারীদের আনুগত্য থাকতেই হবে। পুলিশ এই নীতির বাইরে নয়। কিন্তু,যাঁরা ভাবেন সরকার বেআইনি কাজ সমর্থন করবেন। সেটা কিন্তু নয়। একজন পুলিশ সুপার কোনটা অন্যায় আর কোনটা নয় সুবিচার করার জন্য যথেষ্ট।
ভারত বহুদলীয় রাজনীতিতে যে বিশ্বাসী। নিত্য শুনতে হয় ব্রজবুলি। কেউ সামগ্রিক ভাবে সমাজ জীবনের বৈষম্য গুলি দূর করে, আর্থসামাজিক ব্যবস্থা নিয়ে, জাতি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে কথা বলা, সামাজিক জীবনের অভাব, অভিযোগ এসব নিয়ে কথা বলেন না। তাঁদের নিত্য কাজ সরকারে বিরুদ্ধে সমালোচনা করা। যাঁরা এই কাজ করেন, তাঁরা কিন্তু রাজসুখেই আছেন। সবাই দলগত আদর্শের কথা বলে, পশ্চিম বঙ্গের সামগ্রিক উন্নতিকল্পে কোন চিন্তা করা বা সংসদে তুলে ধরেন না। ভোট সর্বস্ব রাজনীতি আমাদের সর্বনাশের কারন।
পুলিশ সংস্কার কেন্দ্রীয় সরকার কবে করবেন, সেটা অনিশ্চিত। পুলিশের নীচু তলায় প্রচুর চাপ। চাপ এত বেশী যে পুলিশ নুয়ে পড়েছে।
মহামান্য আদালত খুব ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই সিবিআই কে তদন্ত তুলে দিয়েছেন। কিন্তু, সামগ্রিক ভাবে বৃহৎ সমাজে পুলিশের উপর আস্থা ফিরে কি না,আগামী দিন বলবে।
লেখক অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি পুলিশ সুপার ও আইনজীবী।